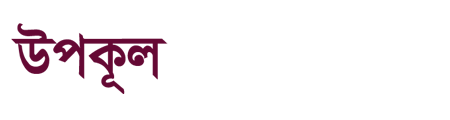[পর্ব-২]
ভাইয়া আমাকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন। মা জিজ্ঞাস করলেন, ভয় পেয়েছি কি না? আমি কোনো জবাব দেইনি। মাটির চুলাই রান্না করলে পাতিলের নিচে কালির আস্তর পড়ে। মা সে কালির সঙ্গে লবণ মিশিয়ে আমার মুখে দিলেন। এরপর থেকে ভাইয়া তো নয়, পরিবারের আর কেউ কোনোদিন আজ পর্যন্ত আমাকে শাসন করেননি। আমার জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত আমার মতো করেই বাস্তবায়িত হয়েছে। এর ফলে স্বাধীন ছিলাম কিন্তু জীবন চলার পথ কখনো মসৃণ হয়নি। জীবনকে সুন্দর করে সাজানোর জন্য গুরুজন ও বড়দের স্নেহ ভালোবাসার পাশাপাশি শাসনও দরকার। এই শিক্ষা যখন পেলাম, ততদিনে অনেক পথ পেরিয়ে এসেছি। মানুষের গড় আয়ু হিসাব করলে জীবনরেখার উল্টো ইউটার্নের নিচের দিকে আমি। বুঝতেই পারছেন, জীবন গঠনের সময়টা অনেক পেছনে রেখে আসছি।
তখন শীতকাল ছিল। আমার বয়স চার বা তার আশেপাশে। বাবা একদিন আমায় সাজিয়ে বাড়ির দরজায় মসজিদ সংলগ্ন মোক্তবে নিয়ে গেলেন। পরনে লুঙ্গি, গায়ে জামা, মাথায় টুপি, পায়ে চপ্পল। সবই নতুন। হাতে বসার জন্য মায়ের হাতে বানানো বটনি(মাদুর)। আমার তেমন কোনো উত্তেজনা নেই। মৌলবি সাহেব(জনাব মোস্তফা হুজুর) আমার চেনা মানুষ। বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে দেখছি তিনি আমাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করেন। হুজুরকে আপ্যায়নের দায়িত্তটা আমার ছিল। আমি হুজুরকে সালাম দিলাম। বাবার কথামতো কদমমুছি করলাম। হুজুর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন। বাবা বিদায় নেওয়ার সময় হুজুরকে বললেন ‘গোস্ত আমনের আর আঁড্ডিগেন আঁরলায় রাইগবেন।’ (গোস্ত আপনার আর হাড়গুলো আমার জন্য রাখবেন)। মোস্তফা হুজুর আমার প্রথম ও শেষ ধর্মীয় শিক্ষক।
মোক্তবে প্রায় শখানেক শিক্ষার্থী হবে। তবে গ্রুপ করা। একেক গ্রুপে ছয় থেকে দশজন করে আছে। গ্রুপের সবার একই পাঠ। সবাইকে বর্গাকারে বসানো হতো। হুজুর সবার মাঝখানে। সব গ্রুপের ছবক দিয়ে হুজুর তার নির্ধারিত আসনে বসে কাঁচন পড়া বানাতেন, কখনো বা সিরামিকের প্লেটে রঙিন কালি দিয়ে বাঁশের কলম দিয়ে তাবিজ লিখতেন। আমার মনে হতো মানুষের যেকোনো অসুখ হলে হুজুরদের ঝাড়ফুঁকে আর তাবিজে ভালো হয়ে যায়। সম্ভবত এ ধারণা তখনকার সময় সমগ্র গ্রাম বংলায় বদ্ধমূলছিল। এ কারণে এদেশে পীর আর মাজার ব্যবসা এত জমজমাট। হুজুর যখন তাবিজ লেখায় মগ্ন আমরা তখন দুষ্টমিতে মত্ত। সবার পড়ার আওয়াজ যখন মৃদু হয়ে আসতো তখন হুজুর চেঁচিয়ে উঠেতেন। মাঝেমাঝে তার তিনফুট লম্বা বেত দিয়ে সরকারি মার দিতেন। এ সময় বাঁচার জন্য পিঠের ওপর চাদর ডাবল করে দিতাম।
রাত তিনটার দিকে সেই কাইয়ের সঙ্গে নারকেল কুচি দিয়ে কলা পাতায় মুড়ে পানি বাষ্পের ওপর দেওয়া হতো। এই কর্মযজ্ঞ সারারাত হয়ে সকালে প্রায় আটটা পর্যন্ত চলতো।
যাহোক আমার কোনো গ্রুপ নেই। যারা কোরআন পড়ে তাদেরও কোনো গ্রুপ নেই, তবে সিনিয়র হিসেবে আলাদা সম্মান আর ক্ষমতা আছে। কারণ হুজুর মাঝেমধ্যে সিনিয়রদের ওপর দায়িত্ত দিয়ে তার দক্ষিণের চরের বাড়ি যেতেন। আমার বড় ভাই খাইরুল আলম কোরআনের ছাত্র। আরও দুই তিনজন আছেন। আমাকে ভাইয়ার পাশে বসানো হলো। আমার প্রথম পাঠ সুরা ফাতিহা শেষ করলাম দু’দিনে। আমার মাথায় সিনিয়র হওয়ার নেশা চাপলো। আমি পাঠে মনোযোগ দিলাম। কখনো কখনো ভাইয়ার সাহায্য নিতাম। মাসখানেকের মধ্যে আমি সব সুরা মুখস্ত করে ফেলি। এরপর হুজুর আমাকে কায়দা দিয়ে একটা গ্রুপে দিলেন। গ্রুপের কচ্ছপ গতির পড়া আমার ভালো লাগেনি। আমি হুজুরকে বলে আলাদা পড়তে লাগলাম। কোথাও সমস্যা হলে ভাইয়ার সাহায্য নিতাম। এক বছরের মাথায় আমি কায়দা আমপারা শেষ করলাম। ততদিনে ভাইয়া বিদায় নিলেন। আমার বড় বোন সালমা, ভাগ্নে আলো, মানিক কোরআন পড়ে।
আমাদের বাড়ির একটা রেওয়াজ ছিল। প্রতিবছর শীতের সময় নতুন ধানের চাল দিয়ে শিরনি রান্না করে মোক্তবের সব শিক্ষার্থীর খাওয়ানো। বাবারা চার ভাই। তাই প্রতিবছর চার দিন চার ঘরে এই আয়োজন হতো। আমাদের বড় উঠানে সবাইকে বসিয়ে মাটির বাসনে খেতে দেওয়া হতো। খবর পেলে আশেপাশের কিছু গরিবও আসতো। আমিও ওইদিন বন্ধুদের সঙ্গে মাটির বাসনে খেতাম। কোনো চামচ ছাড়া হাত দিয়েই খেতাম। এছাড়া যখন রোপা আমন ধানের সিজনশেষ হতো, তখন জালা পীঠা বানানো হতো। এসময় নিকট আত্মীয়াদের সবাইকে দাওয়াত দেওয়া হতো। যে রাতে পীঠা বানানো হতো, তার আগের দিন সব কিছু জোগাড় করে রাখা হতো। সকালবেলা ছোটরা পুকুর পাড়ের কলাগাছ থেকে কলাপাতা সংগ্রহ করতাম। বিকালে নারকেল ভাঙতাম। এ সময় আমাদের ভাইদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হতো। সবাই মিলে চল্লিশ-পঞ্চাশটি নারকেল ভেঙে দা দিয়ে কোরানো হতো। কোরানোর কাজটি বাবার চেয়ে ভালো কেউ পারতাম না। এরপর এগুলোকে কুচি করে রাখা হতো। ধানের জালার (অঙ্কুরিত ধানবীজ) রস দিয়ে চালের গুঁড়ার কাই তৈরি করে সন্ধ্যাবেলা রেখে দেওয়া হতো। রাত তিনটার দিকে সেই কাইয়ের সঙ্গে নারকেল কুচি দিয়ে কলা পাতায় মুড়ে পানি বাষ্পের ওপর দেওয়া হতো। এই কর্মযজ্ঞ সারারাত হয়ে সকালে প্রায় আটটা পর্যন্ত চলতো। সকালে চলতো আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে বিতরণের কাজ। আগে বাড়িতে চাচা-জেঠাদের ঘরে। তারপর অন্যদের জন্য।
আজকে আমাকে কোরআন দেবে। মা হুজুরের জন্য পিঠাপুলি, ডিমের পিঠা আর শিক্ষার্থীদের জন্য মালপোয়া পিঠা বানালেন। তখন যেকোনো শিক্ষার্থী কোরআন ছবক নেওয়ার সময় সাধ্যমতো সবাইকে আপ্যায়ন করাতো। মাকে পা ছুঁয়ে সালাম করে মক্তবের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। বাবা নতুন কোরআন শরিফ আর রেহেল আমার হাতে দিলেন, পিঠার বলটি নিজের হাতে নিয়ে আমাকে হুজুরের কাছে নিয়ে গেলেন। হুজুর আমাকে তার সামনে মুখোমুখি বসালেন। কোরআন শরিফ খুলে বিসমিল্লাহ পড়ে ছবক দিলেন। আমার পাশে বসা বাবার হাসিমাখা মুখখানা এখনো ছবির মতো ভাসছে। সন্তানের সাফল্যে সব বাবা মা এমনিতেই খুশি হন। বাবার খুশি হওয়ার ধরনটা ছিল অচেনা। মনে হয় ভাবছিলেন একরোখা ডানপিঠে স্বভাবের ছেলেটাকে নিয়ে আর চিন্তা নেই। কিন্তু আমার মাথায় যে ওস্তাদ হওয়ার নেশা, সেটা বাবা কী করে জানবেন? হুজুর দোয়া-দরুদ পড়ে দু’হাত তুলে আমিসহ মসজিদ সংলগ্ন কবরের সব মরহুমের জন্য দোয়া করলেন। বাবা হুজুরের হাতে কিছু টাকা দিয়ে আমার প্রতি খেয়াল রাখতে বললেন। আজ বাবা শাসনের কথা বললেন না। আমার নিকট আজ ভিন্ন রকম অনুভুতি কাজ করছে। আজ থেকে আমি সিনিয়র ছাত্র।
বেঁচে থাকুক পৃথিবীর সব মামা-ভাগিনা, বেঁচে থাকুক পৃথিবীর সব আত্মীয়তার বন্ধন।
ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘুম ভেঙে যেতো। আমরা ছোবহে সাদিকের আলোর অপেক্ষায় থাকতাম। এরপর বেরিয়ে পড়তাম ঝরেপড়া আম কুড়ানোর জন্য। এনিয়ে আমাদের সমবয়সীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলতো। কোচা ভরে আম নিয়ে আসতাম আর সবচেয়ে ভালো আমটি টিপেটিপে নরম করে নিচের দিকে ছোট ফুটো করে খেতে খেতে মক্তবে চলে যেতাম। মাঝেমাঝে আমের পোকা মুখে চলে আসতো। মক্তবের পূর্বদিকের রাস্তার পাশের খেজুর গাছের নিচের ছায়াযুক্ত জায়গাটি ছিল সবার পছন্দের। এই নিয়ে অনেক ঝগড়া হতো। অনেক সময় হুজুরের কাছে নালিশও যেতো। আমি এর জন্য একবার বেতও খেয়েছি। এরমধ্যে আমি এক খতম কোরআন শেষ করেছি। পুনরায় হুজুরকে পড়ে শোনাচ্ছিলাম, পাশাপাশি কিছু বইও দিয়েছিলেন (মাদ্রাসার দ্বিতীয় শ্রেণির)।
একদিন হুজুর আমাকে দায়িত্ত দিয়ে চরের বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। আমি সব গ্রুপে ছবক দিয়ে নিজের জায়গায় বসলাম। সবাই ঠিকমতো পড়ছিল। কিন্তু একটা গ্রুপ যারা আগে আমার সিনিয়র ছিল, খুব বেশি বিশৃঙ্খলা তৈরি করছিল। আমি অনেকবার বলার পরও শোনেনি। হুজুরের বিলম্ব হওয়ায় আমি পড়া আদায় শুরু করলাম। যারা পড়া দিতে পারেনি তাদের মাঝখানে জড়ো করলাম।(বিশৃঙ্খলাকারী গ্রুপের কেউই পারেনি)। তারপর মসজিদের পাশের পেয়ারা গাছের একটা ডাল এনে শাস্তি দিলাম। দু’তিন জন আওয়াজ করে কাঁদছিল। আমি সবাইকে ছুটি দেওয়ার জন্য দরুদ পড়তে বললাম। কিন্তু আমার মন্দ কপাল! ঠিক সময়ে হুজুর উপস্থিত। সবকিছু শোনার পর শুধু বলেছিলেন, ‘তুই কি হুজুর অঁয় গেছতনি?’এরপর আমার হাতের সে পেয়ারা গাছের ডাল দিয়ে…। এরপর আর কোনোদিন মক্তবে যাইনি। হুজুরের আশেপাশেও ঘেঁষতাম না।
ছোটকাল থেকেই নানা-নানি, মামা-মামি, খালা-খালু এই সম্পর্কগুলোর প্রতি আমার প্রচণ্ড দুর্বলতা। এখনো আমি মামা-ভাগ্নে সম্পর্ক নিয়ে পাগলপারা। এর কারণ মায়ের কাছ থেকে শুনেছি সত্তরের বন্যার পর আমার একখালা ছাড়া মায়ের নিজের কোনো ভাই-বোন বেঁচে ছিলেন না। মায়ের আত্মীয় সম্পর্কীয় এক খালাতো ভাই, এক চাচা, চারজন ভাগ্নে আর একভাগ্নি ছিলেন। মা আর খালাকে মায়ের খালাত ভাই আবদুল মজিদ নাইয়ুর (বেড়াতে) নিতেন।
সম্ভবত আমি তখন তৃতীয় শ্রেণিতে সকালবেলা খাবার টেবিলের এককোণে বসে হোমওয়ার্ক করছিলাম। এমন সময় একজন বয়স্কলোক সঙ্গে প্রায় আমার বয়সী একটা ছেলেসহ ঘরে প্রবেশ করলেন। লোকটিকে বেশ পরিপাটি ও মার্জিত মনে হলো। আ মি সালাম দিয়ে তাকিয়ে থাকলাম। সালামের জবাব দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাস করলেনম হাজিসাব তোমার কী হয়? আমি বললাম, বাবা। তখন তিনি মুচকি হাসি দিয়ে বললেন। আমি তোমার মজিদ মামা। তোমার মাকে ডাকো। মামা শব্দটা শুনতেই মনের মধ্যে একটা আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো। আর তার সঙ্গে আসা ছেলেটি আজকের মিজান বিন মজিদ। আমি ভেতরে গিয়ে মাকে খবর দিতেই মা মাথায় গোমটা টেনে মামার কাছে আসলেন। সালামের পর পরস্পর কুশল বিনিময় করলেন। আমি তখন খুব বেশি লাজুক স্বভাবের ছিলাম। অনেক চেষ্টার পরও মামা আর মিজানের সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। মা আমাদের চেঁই হিডা (সুটকি পিঠা) আর ভাত খেতে দিয়েছিলেন।
প্রায় দু’বছর পর গ্রীষ্মকাল। চারদিকে পাকা আমের ঘ্রাণ।সকাল দশটা হবে। মা বললেন, তোর মজিদ মামার অসুখ, চল দেইখতে যামু। হাতে মিসরি, বিস্কুট নিলেন। আমরা প্রায় সাড়ে দশটার সময় মামাদের উঠানে গিয়ে পৌঁছলাম। ছোট মামি (মিজানের মা) এসে মাকে জড়িয়ে ধরে মোলাকাত করলেন। আমাদের মামার ঘরে নিয়ে গেলেন। মামা বিছানায় শোয়ানো। অস্থিচর্মসার মামার দেহ, পোশাক আর বিছানা কি পরিপাটি আর পরিচ্ছন্ন! দুপুর বারোটার সময় মিজানের বড় ভাই মামাকে গোসল করানোর জন্য পাঁজাকোলে করে উঠানে একখানা বড় পিঁড়ির ওপর নিয়ে বসালেন। পরম যত্নে মামাকে সাবান মেখে গোসল দিয়ে ঘরে নিয়ে এলেন। আমি এই ফাঁকে ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মিজানের পড়ার ঘরে গেলাম। দুই একটা বই খুলে দেখি মাদ্রাসার বই। মিজান একবার ঢুঁ মেরে চলে গেছে। আমার সঙ্গে কোনো আলাপ হয়নি। মামির ডাকে দুপুরের খাবার খেতে গেলাম। মামির আথিতীয়তায় আমরা মুগ্ধ। আসরের সময় আমরা মামার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়ালাম। আসার পথে মা বললেন, ‘তোর মামারে যে গোসল করাইছে, হেতে তোর মামার সৎ পুত। আইজকাইল নিজের হোলা মাইয়াও তো বাপ মার এরকম যত্ন করে না।’ বেঁচে থাকুক পৃথিবীর সব মামা-ভাগিনা, বেঁচে থাকুক পৃথিবীর সব আত্মীয়তার বন্ধন।
চলবে…